উত্তর :-
উত্তর : ভূমধ্যসাগর : আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগর দ্বারা বেষ্টিত বিশাল ভূভাগ হল আফ্রিকা মহাদেশ। মানবসভ্যতার আদি জন্মভূমি ও কার্থেজ সভ্যতার পীঠস্থান আফ্রিকা ইউরোপের নিকটবর্তী হলেও ইউরোপীয়দের কাছে তা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ‘অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ” (Dark Continent) নামে পরিচিত ● আফ্রিকায় অভিযান : পঞ্চদশ শতকের পরে ইউরোপের সামুদ্রিক জাতিগুলি আফ্রিকার উপকূলের বিভিন্ন অঞ্চলে এসে পৌঁছালেও আফ্রিকা তাদের কাছে অজানাই ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকে নানা কারণে আফ্রিকার গুরুত্ব প্রকাশ পায়। নেপোলিয়ন কর্তৃক মিশন অধিকার এবং পরবর্তীকালে মিশন থেকে ইংল্যান্ড কর্তৃক ফরাসি সেনা বিতাড়ন প্রভৃতি ব্যাপারে আফ্রিকার গুরুত্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি উপলব্ধি করে। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডে দাসব্যবসা বন্ধ হলে খ্রিস্টান মিশনারিগণ আফ্রিকায় এসে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে এবং খ্রিষ্টধর্মের সপক্ষে প্রচার চালান। এছাড়া বিভিন্ন অভিযাত্রীরা তাদের আফ্রিকা অভিযানের কথা লিখতে থাকেন। এই সময়ে আফ্রিকার আলজেরিয়া ছিল ফরাসি উপনিবেশ এবং দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ, কেপ কলোনি ছিল ইংল্যান্ডের দখলে। টিউনিস ও ত্রিপোলি ছিল তুর্কি সাম্রাজ্যভুক্ত আর বাকি আফ্রিকা ছিল অনাবিষ্কৃত। আফ্রিকা সম্বন্ধে জানার পরেই ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে আফ্রিকা সম্পর্কে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। অল্প সময়ের মধ্যেই ইউরোপ আফ্রিকার বাকি দেশগুলিতে নিজ অধিকার কায়েম করতে শুরু করে।
• আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন : আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের ক্ষেত্রে দুটি পর্যায় লক্ষ করা যায়। যথা—(ক) ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন এবং (খ) ঊনবিংশ শতকের সাতের দশক থেকে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত উপনিবেশ বিস্তার।
(ক) প্রথম পর্যায় (ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত)
:
√ (১) ওলন্দাজ উপনিবেশ : ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকায় মাত্র দুটি ঔপনিবেশিক শক্তি ছিল—ওলন্দাজ এবং পর্তুগিজ। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজরা প্রথম কেপ কলোনি দখল করে এবং পরবর্তীকালে সেখানে বসবাস শুরু করে। যদিও পরে কেপ কলোনিতে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপিত হয়, কারণ ওলন্দাজরা ব্রিটিশদের তা বিক্রি করে দেয়। এছাড়া নাটাল, অরেঞ্জ নদী উপত্যকা অঞ্চল এবং ট্রান্সভালে ওলন্দাজ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ব্রিটিশরা যুদ্ধের দ্বারা সেগুলিও দখল করে নেয়।
/ (২) পর্তুগিজ উপনিবেশ: বার্থোলেমিউ দিয়াজ, ভাস্কো ডা গামা প্রমুখ দুঃসাহসিক পর্তুগিজ নাবিকদের প্রচেষ্টায় দক্ষিণ আফ্রিকায় পর্তুগিজ আধিপ্ত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আফ্রিকায় গিয়ানা উপকূল, শোফালা এবং অ্যাঙ্গোলায় পর্তুগিজদের তিনটি উপনিবেশ গড়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই উপনিবেশগুলি ছিল প্রধানত দাসব্যবসার কেন্দ্র / (৩) ফরাসি উপনিবেশ : ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে আফ্রিকার আলজেরিয়া ছিল ফরাসিদের উপনিবেশ।
→(খ) দ্বিতীয় পর্যায় (ঊনবিংশ শতকের সাতের দশক থেকে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত) : এই পর্ব থেকে আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তারের প্রতিযোগিতা আরও তীব্র আকার ধারণ করে। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার ১/১০ অংশ ছিল ইউরোপীয় উপনিবেশ, মাত্র ২০ বছরের মধ্যে যা ৯/১০ অংশে পরিণত হয়।
√ (১) বেলজিয়ান উপনিবেশ : আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে বেলজিয়ামরাজ দ্বিতীয় লিওপোল্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। অভিযাত্রী স্ট্যানলি-র কঙ্গো আবিষ্কার বেলজিয়ামরাজকে প্রলুব্ধ করে। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল—পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ভূগোলবিদদের সাহায্যে আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগকে উন্মুক্ত ও সভ্য করা। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক হয় ‘আন্তজাতিক আফ্ৰিকা সমিতি'। কঙ্গোর বিশাল অঞ্চল নিয়ে তিনি ‘কঙ্গো ফ্রি স্টেট' গঠন করেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই উপনিবেশে তাঁর ব্যক্তিগত অধিকার ছিল। পরবর্তীকালে বেলজিয়াম সরকারকে তিনি তা হস্তান্তর করেন।
বেলজিয়াম কঙ্গো উপত্যকা দখল করলে আফ্রিকার বণ্টন ত্বরান্বিত হয়। বেলজিয়ামকে দেখে উৎসাহিত হয়ে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল, জামানি, ইতালি ও স্পেন আফ্রিকায় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হয়।
√ (২) ব্রিটিশ উপনিবেশ : আফ্রিকার বৃহৎ অংশে ইংল্যান্ডের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাচদের কাছ থেকে কেপ কলোনি, নাটাল ও অরেঞ্জ রিভার কলোনি এবং বুয়রদের পরাজিত করে ট্রান্সভাল ইংল্যান্ডের দখলে আসে। আফ্রিকার দক্ষিণে অবস্থিত এই সকল অঞ্চলগুলিকে একত্রিত করে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় 'দক্ষিণ আফ্রিকা সংগঠন। উত্তরে মিশর অধিকার করার ফলে ইংল্যান্ডের আধিপত্য সুদান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পূর্ব আফ্রিকা ও উগান্ডা এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে জাম্বিয়া, গোল্ড কোস্ট, নাইজেরিয়া, সোমালিল্যান্ড ইত্যাদি ইংল্যান্ডের অধিকারে আসে।
√ (৩) ফরাসি উপনিবেশ : ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স টিউনিশিয়া দখল করে। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে কঙ্গো নদীর দক্ষিণ উপকূল অধিকার করে ফ্রান্স চাদ হ্রদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এরপর একে একে মাদাগাস্কার দ্বীপ (১৮৯৬ খ্রি.),মরক্কো (১৯১২ খ্রি.), সমগ্র সাহারা ফ্রান্সের দখলে চলে যায়। এইভাবে উত্তর আফ্রিকায় ফ্রান্সের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
√ (৪) পর্তুগিজ উপনিবেশ : পর্তুগিজরা বেলজিয়াম কঙ্গোর দক্ষিণ উপকূলের অ্যাঙ্গোলা এবং পশ্চিম উপকূলের মোজাম্বিক দখল করে। অ্যাঙ্গোলার নাম হয় ‘পর্তুগিজ পশ্চিম আফ্রিকা' এবং মোজাম্বিকের নাম হয় ‘পর্তুগিজ পূর্ব আফ্রিকা'।
/ (৫) জার্মান উপনিবেশ : জার্মানি প্রথমে আফ্রিকায় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল না। কিন্তু জার্মান শিল্পপতিদের চাপে বিসমার্ক বাধ্য হয়ে আফ্রিকার চারটি অঞ্চল, যথা—দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা, ক্যামেরুন এবং টেগোল্যান্ড জার্মান উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেন।
√ (৬) ইতালিয় উপনিবেশ : ইতালি ইরিত্রিয়া ও সোমালিল্যান্ডের কিছু অংশ দখল করে। স্যাডোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে আবিসিনিয়া দখল করতে ব্যর্থ হলেও তুরস্কের অধীনস্থ ত্রিপোলি ও সাইরেনেইকা দখল করে পরবর্তীকালে যদিও মুসোলিনি (Mussolini) আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়াকে ইতালিয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন।
√ (৭) স্পেনীয় উপনিবেশ : রিও ডি ওরো নামে একটি প্রদেশ এবং জিব্রাস্টার প্রণালীর বিপরীত দিকের কিছু স্থান স্পেন দখল করেছিল।
• আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের ফলাফল : আফ্রিকা মহাদেশে ইউরোপীয় শক্তিগুলির উপনিবেশ স্থাপনের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।
(১) পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব : আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অংশে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি উপনিবেশ স্থাপন করে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটায়। এর ফলে আফ্রিকার অনুন্নত অঞ্চলগুলি সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোয় ক্রমশ আলোকিত হয়ে উঠতে থাকে।
(২) কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের উপর অত্যাচার : সমগ্র আফ্রিকা ইউরোপের উপনিবেশে পরিপ্ত হওয়ার ফলে আফ্রিকার মানুষ তাদের স্বাধীনতা হারিয়েছিল। ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ মানুষদের তাচ্ছিল্য, অপমান এবং সীমাহীন অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছিল তারা। ইউরোপীয়দের এই পরাধীনতার পাশ ছিন্ন করতে আফ্রিকাবাসী দীর্ঘ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল।
→(৩) ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার বিরোধ : আফ্রিকায় উপনিবেশ দখলকে কেন্দ্র করে ইউরোপের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির মধ্যে পরস্পরের প্রতি তীব্র বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়। মিশর ও সুদান অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এ ছাড়া ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে মরক্কোকে এবং ইটালি ও ফ্রান্সের মধ্যে টিউনিশিয়াকে কেন্দ্র করে বিরোধ বাধে।
=====================
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
প্রশ্ন: অ্যানাব্যাপটিস্ট আন্দোলন
উত্তর :- ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন ছিল অশান্ত ও অস্থির। এই সময় ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হলে নতুন নতুন ধর্মমতের উদ্ভব ঘটেছিল। নতুন গড়ে ওঠা ধর্মমত বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকটি ছিল র্যাডিক্যাল বা চরমপন্থী। এই চরমপন্থী গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম ছিল অ্যানাব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়। খ্রিস্ট্রিয় প্রথম শতকে প্রচারিত চার্চের মূল নীতি ও আচার আচরণের মধ্যে খ্রিস্টের মূল আদর্শ নিহিত আছে। তারা মনে করেন চার্চ হল বিশ্বাসীদের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। জার্মানি এবং ইওরোপের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়া অ্যানাব্যাপটিস্টরা এই ধরনের মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।
এই আন্দোলনের অন্যতম আদি প্রবক্তা ছিলেন অধ্যাপক কার্লসটাড। তিনি প্রথমদিকে লুথারের সহযোগী ছিলেন। কিন্তু পরে লুথারের মধ্যপন্থী নীতি ত্যাগ করে বৈপ্লবিক ধর্মসংস্কারের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। কার্লসটাড ছাড়াও যাদের হাত ধরে দেশে দেশে অ্যানাব্যাপটিস্ট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য ছিলেন ডেভিড জোরিস, কনরাড গ্রেভেল, জেকব হুটার, বালসার হামেয়ার প্রমুখ। অ্যানাব্যাপটিস্ট আন্দোলনের এইসব নেতারা কখনও মেনে নিতে পারেননি যে চার্চ ও সমাজ হল সমর্থক!
নেদাবল্যান্ডে অ্যানাব্যাপটিস্টদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এখানে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডেভিড জোরিস, যিনি আদতে ছিলেন কবি ও শিল্পী। উগ্র অতিন্দ্ৰীয়বাদে বিশ্বাসী এই কবি ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে 'Book of Wonders' নামক পুস্তিকার মাধ্যমে প্রচার করেন যে, মানুষের ধর্মবিশ্বাস তার হৃদয়ের অনুভূতি, বাইরের আচার অনুষ্ঠান নয়। যারা ধর্ম আলোচনা করেন এবং মানুষকে শাস্তি দেন বা অত্যাচার করেন তারা প্রকৃত ধার্মিক নন। তবে মুনজেরের ন্যায় জোরিসের যাত্রাপথও মসৃণ ছিল না। তিনি পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করলেও তার পরিবারকে হত্যা করা হয়। বাকি জীবন তিনি বাসেলে ছদ্মনামে কাটিয়ে দেন।
• মূল্যায়ন : আপাতদৃষ্টিতে অ্যানাব্যাপটিস্ট আন্দোলনকে লুথারবাদের বিরুদ্ধে র্যাডিক্যাল বা চরমপন্থী বলা হলেও কার্যক্ষেত্রে তা সঠিক ছিল না। কারণ এরা না ক্যাথলিক, না প্রোটেস্ট্যান্টদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করেছিল। বরং অতি বর্বর ও নৃশংসতার সঙ্গে এই আন্দোলনের নেতাদের যেভাবে দমন করা হয় তা নিশ্চয়ই পাঠকের মনে ঘৃণার উদ্রেক করবে। আবার লুথার বা জু-ইংলি পোপের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন তাকে কোনোভাবেই র্যাডিক্যাল বা চরমপন্থী বলা হয়নি। তার চেয়েও বড় কথা এরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় প্রতিহিংসার নীতি গ্রহণ করেছিলেন।
=====================
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
আরো দেখো 👉
➤ -নবজাগরণ কাকে বলে। সর্বপ্রথম ইতালিতে কেন নবজাগরণের সূচনা হয়। উত্তর দেখো ➤ রেনেসাঁ বা নবজাগরণ বলতে কী বোঝ। শিল্পে নবজাগরণের প্রভাব আলোচনা করো। উত্তর দেখো ➤ ইউরোপে নবজাগরণের প্রভাব বা ফলাফল আলোচনা করো। উত্তর দেখো
=====================
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
প্রশ্নঃ ইউরোপে সামন্তপ্রথার পতন/অবক্ষয় এর কারনগুলি আলোচনা করো
উত্তর :- সামন্তপ্রথা ছিল মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। খ্রিস্ট্রিয় দশম থেকে একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে সামন্তপ্রথার যে চরম বিকাশ ঘটেছিল তা শুরু হয়েছিল খ্রিস্ট্রিয় সপ্তম থেকে অষ্টম শতকের মধ্যভাগে। সামন্তপ্রথার অবক্ষয়ের সূত্রপাত ঘটেছিল খ্রিস্ট্রিয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাবে। এই অবক্ষয়ের কারণগুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল –
√ প্রথমত, সামন্ততন্ত্রের প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষি। জমির মালিকানা থাকত সামন্তপ্রভুদের হাতে। আর ভূমিদাস বা সার্করা বাধ্য থাকত বিনা বেতনে ঐসব জমিগুলিতে চাষাবাদ করতে। ক্রমে নতুন নতুন শহর বা নগর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যও প্রসার লাভ করতে থাকে। ফলে সামন্তপ্রভুদের ছেড়ে ভূমিদাসরা কলকারখানার কাজে নিযুক্ত হতে শুরু করে।
√ দ্বিতীয়ত, দ্বাদশ শতকে যে ধর্মযুদ্ধ বা ক্রসেড শুরু হয়েছিল তাতে বহু সামন্তপ্রভু যোগদান করেছিলেন। এই ধর্মযুদ্ধের ফলে সামন্তপ্রভুদের প্রচুর অর্থব্যয় হয়, এমনকি সামন্তদের অনেকে মারাও যান। জীবিতাবস্থায়, ভগ্নহৃদয়ে কিছু সামন্ত দেশেও ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারা ছিলেন আর্থিক ও মানসিক উভয়দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত।
√ তৃতীয়ত, ধর্মযুদ্ধের পর ইউরোপীয়রা, আরবীয়দের সংস্পর্শে আসে। তাতে আরবীয় জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পচর্চার প্রভাব ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রসার লাভ করে। ফলস্বরূপ ইউরোপবাসীদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। ধীরে ধীরে সামন্তপ্রথার বিরদ্ধে ইউরোপীয় জনসাধারণের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।
√ চতুর্থত, শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ লাভের ফলে সমাজে শিল্পপতি ও বণিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এরা শক্তি সঞ্চয় করতে করতে সমাজে সৃষ্টি করল মধ্যবিত্ত শ্রেণির। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনদর্শন ছিল সামন্তপ্রভুদের থেকে ভিন্ন ধরনের। এরা যুক্তিবাদী ও কুসংস্কারমুক্ত হওয়ায় এদের সঙ্গে সামন্তদের বিরোধ বাধে।
√ পঞ্চমত, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও সেইসঙ্গে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উদ্ভবের ফলে সামন্তদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট হতে থাকে।
• মূল্যায়ন : উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে একাধিক কারণে সামন্তপ্রথার অবসান ঘটে। সামন্তপ্রথার পতনের সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন অর্থনীতির বিকাশ ঘটে যার ফলে আধুনিক যুগের ঊষালগ্ন সূচিত হয়েছিল।


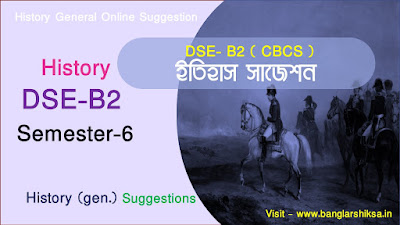








No comments